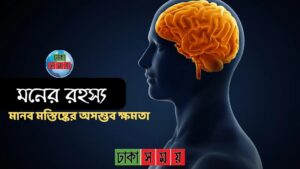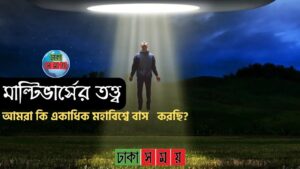বাংলাদেশ বনাম ভারত : কে জিতবে যুদ্ধে ?
বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ এবং সামরিক উত্তেজনার আবহে ভারত ও বাংলাদেশকেও ঘিরে উঠছে নানা আলোচনা। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন ও স্বাধীন অবস্থানকে কেন্দ্র করে কিছু বিশ্লেষক দাবি করেছেন, ভারত বাংলাদেশের উপর সামরিক আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা করছে। যদিও এ ধরনের বক্তব্য অনেকেই রাজনৈতিক উস্কানি বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন, তবুও সামরিক বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
ভারতের সামরিক শক্তি
ভারত বর্তমানে পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম সামরিক শক্তিধর দেশ। ভারতীয় সেনাবাহিনীর মোট সদস্য সংখ্যা প্রায় ১৩ লাখ, যার একটি বড় অংশ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষায় নিযুক্ত। কাশ্মীর থেকে শুরু করে ভারতের পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যে (যেগুলো ‘সেভেন সিস্টার’ নামে পরিচিত) বিভিন্ন বিদ্রোহ দমনে ভারতীয় সেনাদের ব্যস্ত থাকতে হয়। সেই সঙ্গে পাকিস্তান ও চীনের মতো প্রতিবেশীদের মোকাবিলায় ভারত সর্বদা সতর্ক অবস্থানে থাকে।
ভারতের বিমান বাহিনী পৃথিবীর অন্যতম আধুনিক শক্তি হিসেবে বিবেচিত হলেও লজিস্টিক সহায়তার অভাবে এর কার্যকারিতা অনেক ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হয়। বর্তমানে ভারতের কাছে প্রায় ৫০০ যুদ্ধবিমান রয়েছে, যার মধ্যে কিছু পুরনো মডেলের। এদিকে ভারতের সীমান্ত এলাকায় চীন ও পাকিস্তানের ক্রমাগত চাপের কারণে বিমানবাহিনীর আধুনিক যুদ্ধবিমানের বেশিরভাগই সেসব অঞ্চলে মোতায়ন থাকে। ফলে বাংলাদেশে আক্রমণ করার মতো পর্যাপ্ত সামরিক সংস্থান সংগ্রহ করা ভারতের জন্য সহজ হবে না।
বাংলাদেশের সামরিক প্রস্তুতি
বাংলাদেশ সামরিক দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ার একটি শক্তিশালী দেশ হিসেবে নিজেদের অবস্থান তৈরি করছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা যেমন উল্লেখযোগ্য, তেমনি তাদের পেশাগত দক্ষতাও আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের অধীনে বাংলাদেশি সেনারা প্রায় ৪৩টি দেশে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।
সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ অত্যাধুনিক সামরিক সরঞ্জাম সংগ্রহে মনোযোগ দিয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য তুরস্ক থেকে কেনা অত্যাধুনিক ড্রোন এবং চীনের উভচর ট্যাংক। এ ধরনের সরঞ্জাম বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করেছে। বাংলাদেশ সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণের জন্য আরও বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।
সম্ভাব্য সংঘর্ষের ফলাফল
বিশ্লেষকদের মতে, ভারত বাংলাদেশের মতো একটি দেশকে দখল করতে চাইলে তাদের নিজেদের শক্তির তুলনায় তিন গুণ বেশি সৈন্য মোতায়ন করতে হবে। তবে বাংলাদেশের ভূখণ্ড এবং জনগণের প্রতিরোধ ক্ষমতা এমন একটি অভিযানের সম্ভাবনা কার্যত অসম্ভব করে তুলেছে।
এদিকে, ভারত যদি বাংলাদেশের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, তবে চীন ও পাকিস্তানের মতো প্রতিবেশীরা এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে ভারতের ওপর আক্রমণ চালাতে পারে। এমনকি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে, যা সেভেন সিস্টার অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে আরও উসকে দেবে।
বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা
বক্তারা জোর দিয়ে বলেছেন, যুদ্ধ কখনও কোনো সমস্যার সমাধান হতে পারে না। ভারত ও বাংলাদেশের জনগণের উচিত এমন কোনো পদক্ষেপ এড়িয়ে চলা, যা দুই দেশের মধ্যে শত্রুতার সম্পর্ক সৃষ্টি করে। বরং সহযোগিতা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে উভয় দেশের উন্নয়নে মনোযোগ দেওয়া উচিত।
যদি যুদ্ধ হয়, তা হলে শুধু দুটি দেশই নয়, পুরো অঞ্চলের স্থিতিশীলতা হুমকির মুখে পড়বে। তাই আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের গুরুত্ব সর্বাধিক।